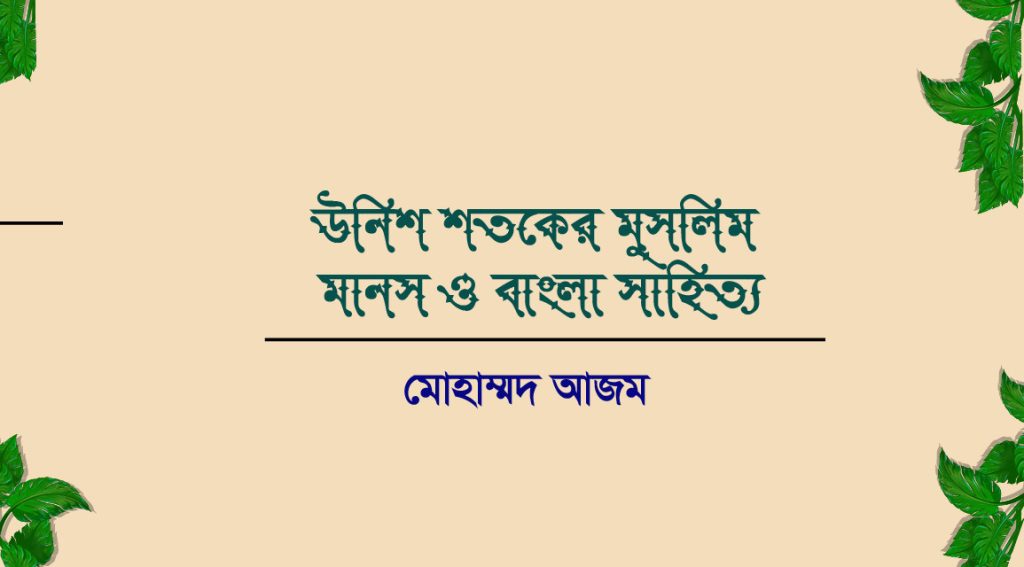
মোহাম্মদ আজম
শিরোনামের ‘মুসলিম’ শব্দটির ব্যাপারে প্রথমেই টীকা দিয়ে রাখা দরকার। ‘বাংলা সাহিত্য’ কথাটার উপস্থিতিতে এ-ধরনের অনুমান হওয়া সম্ভব যে, এখানে বাংলাভাষী মুসলমানের কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু বাংলা অঞ্চলে অবাঙালি মুসলমানের সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং তারাই ছিল প্রভাবশালী। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলাপ তুললে আলোচনার কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার কথা মনে না এসে উপায় থাকে না। তখন কলকাতাই ছিল বাংলা সাহিত্যের, অন্তত আধুনিক অর্থে আমরা যাকে বাংলা সাহিত্য বলে প্রায় সর্বসম্মত স্বীকৃতি দিয়েছি, তার প্রধানতম চর্চাস্থল। সে-কলকাতায় বাঙালি মুসলমানের তুলনায় উর্দুভাষী মুসলমানরা কেবল সংখ্যায় নয়, প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকেও বেশ অগ্রসর ছিল। এমতাবস্থায় ‘বাংলা সাহিত্যে’র সাপেক্ষে আলাপ তুলে আমরা বাঙালি মুসলমানকে যতই আলাদা করতে চাই না কেন, দুটি সংশ্লিষ্ট ও প্রতাপশালী জনগোষ্ঠীর হিস্যা বাদ দিয়ে সে-আলাপ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।
এর প্রথমটি যদি হয় বাংলা অঞ্চলের অবাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়, অন্যটি হবে হিন্দু ভদ্রলোক সমাজ। উনিশ শতকের বাংলা ভাষাচর্চা, সাহিত্যচর্চা এবং পশ্চিমা অর্থে আধুনিকতার চর্চা প্রধানত শেষোক্ত সমাজটিই করেছিল। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এবং চর্চাকারীরা সংখ্যায় খুব কম হলেও সে-চর্চার ফল বর্ণাঢ্য ও ঈর্ষণীয়। বাঙালি মুসলমান সমাজ নিয়ে আলাপে এ-জনগোষ্ঠীর অনিবার্যতা এই যে, মুসলমান সমাজ যখন ‘আধুনিকতা’র সিঁড়িতে পা রাখল, কিংবা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় অগ্রসর হলো, তখন ওই জনগোষ্ঠীর নানামাত্রিক সাপেক্ষতা এড়িয়ে পথ চলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুত, এ-সাপেক্ষতা এত প্রবল যে, এখন প্রায় দুশো বছর পরেও আমাদের প্রভাবশালী বয়ানগুলো একে এড়িয়ে কথা বলতে শেখেনি। সাপেক্ষতার কথা মনে রাখা জরুরি; তার এক বড় কারণ এই যে, বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী হিসেবে আধুনিকায়নের নিরিখে মুসলমান সমাজের বিলম্বিত বিকাশে ভদ্রলোক হিন্দু সমাজের প্রভাব ছিল অতি গভীর। কিন্তু সাপেক্ষতাকেই চূড়ান্ত মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করায় মুসলমান সমাজের বিকাশের নিজস্ব বহু মাত্রার দিকে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ কম হয়েছে। পাঠের সে এক সীমাবদ্ধতাই বটে।
অন্যদিকে, বাংলা অঞ্চলের উর্দুভাষী মুসলমান সমাজের প্রচণ্ড প্রতাপের মধ্যেই বাংলাভাষী মুসলমান বিদ্বৎসমাজের বিকাশ ঘটেছিল। তার সঙ্গে এ-কথাও গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত থাকা দরকার যে, সর্বভারতীয় উর্দু-সংস্কৃতির প্রভাব এড়ানোও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশ শতকের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাস্তবতায় উর্দুর বিপরীতে বাংলাভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের বিকাশের পটভূমিতে অনেকটা কালাতিμমী দোষ ঘটিয়ে বিচার করা হয় বলে উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের উর্দুভাষা-লগ্নতাকে ‘ত্রুটি’ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু যদি ব্রিটিশ ভারতীয় বাস্তবতার পটভূমিতে ভারতীয় মুসলমান সমাজের ‘সংখ্যালঘুতা’ বিবেচনায় রাখা হয়, আর ভারতীয় রাজনীতিতে নিখিল মুসলমান সমাজের ঐক্যের বোধটা উপলব্ধি করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে, বাংলাভাষী মুসলমানের কথিত উর্দুপ্রীতি বিদেশিয়ানা তো নয়ই, এমনকি মুসলমানিত্বও নয়, বরং নির্ভেজাল অস্তিত্বলগ্ন বাস্তবতা। ঠিক যেমন কলকাতার ভদ্রলোকশ্রেণির গত বহু দশকের ইংরেজিয়ানা তার বাঙালিয়ানায় বড় কোনো সংকট তৈরি করেনি।
দুই
তাহলে বাংলা সাহিত্যচর্চার নিরিখে ‘মুসলিম মানস’ শব্দযুগল বাঙালি মুসলমানকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করলেও আরো অন্তত তিনটি বর্গকে হাজির-নাজির জেনেই আলোচনাটা করতে হবে। তার বাইরে ছাতাবর্গ হিসেবে থাকবে মহামহিম ইংরেজ রাজ, যার ছত্রছায়ায় প্রচণ্ড ঔপনিবেশিক বাস্তবতার মধ্যে প্রাগুক্ত প্রতিটি জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিচলন এবং হ্রাস-বৃদ্ধি সংঘটিত হয়েছিল। ঠিক এখানেই ‘উনিশ শতক’ সময়বর্গটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
অনেকেই প্রশ্ন তুলে থাকেন, উনিশ শতক কেন? আমাদের বর্তমান বাস্তবতায় উনিশ শতক কি যথেষ্ট দূরবর্তী নয়? জবাবে বলতে হয়, আমাদের বর্তমানময়তার জন্য উনিশ শতক একমাত্র না হলেও খুবই জরুরি বর্গ। যে-ধরনের আধুনিকায়নের পথ ধরে বাংলাদেশের জনসমাজের গরিষ্ঠাংশ অর্থাৎ মুসলমান সমাজের বিকাশ ঘটেছে, এবং আজতক যে-ধরনের জীবনদৃষ্টি ও ইতিহাসবোধ আমাদের বর্তমানকে সবচেয়ে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তার অধিকাংশ মূল-ধারণা কাঠামোপ্রাপ্ত হয়েছিল উনিশ শতকেই।
ঠিক এ-ধরনের একটা প্রয়োজনবোধের প্রকাশ হিসেবে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এ-সময়ের মুসলমান সমাজ ও বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। আজকের এ-বক্তৃতায় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে স্মরণ করতেই হয়। তার প্রধান কারণ, তাঁর স্মরণেই এ-বক্তৃতা। অন্যতর কারণ, আজকের বক্তৃতার বিষয় আবশ্যিকভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁর ইতোমধ্যে ক্লাসিক হয়ে-ওঠা বইটিকে – মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য নামে যে-বই প্রথমবারের মতো বেরিয়েছিল ১৯৬৪ সালে। এটি অ্যাকাডেমিক গবেষণার সংশ্লিষ্ট এলাকায় দেশে ও বিদেশে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত গ্রন্থ। কয়েক দশক পরে প্রকাশিত গ্রন্থটির এক নতুন মুদ্রণে লেখক জানিয়েছেন, বইটিতে প্রকাশিত মতামত ও বিশ্লেষণ তখনো বিশেষ পরিবর্তন করার দরকার তিনি বোধ করেননি। এই যে কয়েক দশক ধরে তিনি নিজের মতে নিষ্ঠ থাকতে পেরেছেন, আর অন্য ব্যবহারকারীরাও এ-বয়ানে সম্মতি দিয়ে গেছেন, তা একদিকে বইটির শক্তিমত্তার পরিচায়ক, অন্যদিকে পরিবর্তিত তথ্য-উপাত্ত এবং দৃষ্টিভঙ্গি অঙ্গীভূত না করা দু-তরফেই কিছু সীমাবদ্ধতাও নির্দেশ করে। প্রথমে শক্তিমত্তার দিকগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করা যাক।
মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থ-গবেষক আনিসুজ্জামানের তথ্যনিষ্ঠার চমৎকার নিদর্শন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাহিত্যপাঠের কায়দা-কানুন ও দক্ষতা। গবেষকের বস্তুনিষ্ঠ মনও এ-বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আনিসুজ্জামান গবেষণার সীমা নির্ধারণ ও তদনুযায়ী গোছগাছের জন্য সুখ্যাত। এ-বইয়ে সে-খ্যাতির উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি ঘটেছে। এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে গ্রন্থটির গদ্যরীতি আর উপস্থাপনভঙ্গিতে। ফলে বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে।
গবেষণাগ্রন্থ হিসেবে বইটির দ্বিতীয় বড় গুণ বেশকিছু নতুন টেক্সট ও রচনাধারা প্রথমবারের মতো বিশ্লেষিত হওয়া, এবং সেসব বিশ্লেষণের পাঠক-স্বীকৃতি। বলা যায়, সাহিত্যের এবং ইতিহাসের বেশকিছু দিকের পাঠ-পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়েছে এ-বইয়ে, যা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে।
তবে এ-বইয়ের সবচেয়ে বড় গুণ দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের ব্যাপারে স্পষ্টতা আর একাগ্রতা। একনামে একে ডাকতে পারি আধুনিকায়ন নামে। লেখক প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা প্রভাবে আধুনিকায়নের যেসব নতুন আলামত হিন্দু সমাজে ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছিল, মুসলমান সমাজে তার আবির্ভাবের যাত্রাপথ তালাশ করেছেন। উদারনৈতিক মানবতাবাদী ঘরানার কিছু বুনিয়াদি ধারণা, যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থে সেক্যুলারবাদ, সাহিত্যে রুচি-সৌন্দর্য আর মানবিক অভিব্যক্তির অন্বেষণ, দুনিয়াবি দৃষ্টিভঙ্গির μম-অগ্রসরতা অর্থে প্রগতি ইত্যাদি তাঁর যাবতীয় বিবেচনা ও মূল্যায়নে পরম গুরুত্ব পেয়েছে। এ-বইয়ের সবচেয়ে বড় গুরুত্ব এসব জীবনদৃষ্টির পরিচ্ছন্ন ও নিশ্চিত একটা রূপরেখার অধীনে যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত ও মূল্যায়নকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করতে পারা। আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা আর দুনিয়াদারি অর্থে সেক্যুলারবাদ ইত্যাদি বর্গের স্বচ্ছ আর প্রত্যয়ী অধিগ্রহণই সম্ভবত এ-গ্রন্থের দীর্ঘমেয়াদি সম্মতিলাভের মূল কারণ।
অনেকেই বলে থাকেন, ‘মুসলিম মানস’কে আলাদাভাবে চিহ্নিত-চিত্রিত করা বৃহত্তর পাকিস্তানি ভাবধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তাঁর পরবর্তী কাজ মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্রকেও এ-ধারায় বিবেচনা করা চলে। এ-কথা আংশিক সত্য মাত্র। আর আংশিক হিসেবে তা প্রকৃত ‘সত্য’ থেকে এতটাই দূরবর্তী যে, এ-মূল্যায়ন মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য বইটি সম্পর্কে বস্তুত কোনো সত্যই প্রকাশ করে না। সত্য এই যে, ষাটের দশকে যখন বাংলাভাষীরা ইতোমধ্যেই দুই রাষ্ট্রে বিভাজিত, এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র এক উপস্থিত বাস্তবতা, তখন বিশেষভাবে মুসলমান জনগোষ্ঠীর স্বরূপের সন্ধান করা একজন তরুণ গবেষকের কাণ্ডজ্ঞানের পরিচায়ক। জরুরি প্রশ্ন হলো, তখন বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে-ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সঙ্গে এ-বয়ান সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে কি না। এ-প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, মুসলমানপ্রধান এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদী’ ধ্যানধারণা আবিষ্কার করে তাকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার যাবতীয় উপাদান এ-গবেষণাগ্রন্থে হাজির আছে। লেখক মুখ্যত স্বাতন্ত্র্যবাদিতার উপাদানগুলো চিহ্নিত করে তাকে পরিহার করা এবং ইতিহাসে সমন্বয়বাদিতার যেসব বড় মুহূর্ত অঙ্কিত হয়ে আছে, সেগুলোকে সামনে নিয়ে আসার কাজটাই করেছেন। সেখানে সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি, অসাম্প্রদায়িকতা, বাংলা ভাষার প্রমিত রূপের চর্চা এবং সর্বোপরি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলিঙ্গন প্রধান হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যবাদও সেখানে বন্দিত হয়নি, নিখিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শবাদও বড় হয়ে ওঠেনি। ষাটের দশকের পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাদের মডারেট ও গ্রহণযোগ্য একটা রূপই তাতে ধরা পড়েছে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বিখ্যাত উদারনীতিবাদের সে এক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন বোঝাপড়া। উল্লেখ্য, বিশ শতকের আশির দশকে ঢাকায় তুলনামূলক উগ্রবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে বিকাশ ও প্রকাশ দেখি, আনিসুজ্জামান তাতে খুব সামান্যই অংশগ্রহণ করেছেন, যদিও মোটাদাগে নতুন ধারার জাতীয়তাবাদ চর্চাকারীদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বিরোধ ছিল না।
তিন
গত কয়েক দশকে ইতিহাসদৃষ্টি ও তথ্য-উপাত্তের যেসব নতুন আমদানি ঘটেছে, তার একাংশের ওপর এবার নজর দেওয়া যাক।
প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ‘আধুনিকতা’বিষয়ক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের কথা। উনিশ শতকের মুসলিম মানসকে যদি আনিসুজ্জামানের বয়ানের পটভূমিতে পাঠ করতে চাই, তাহলে এ-বর্গের ধারণাগত পরিবর্তন এ-কারণে খুব জরুরি যে, তাঁর পুরো বয়ানের শিরদাঁড়া আধুনিকতার ধারণা। আধুনিকায়নকে তিনি দেখেছেন স্বতঃপ্রগতিশীল এক গুণবাচক বর্গ হিসেবে। সাধারণভাবে আজকাল আর ব্যাপারটিকে সেভাবে দেখা হয় না। না-দেখার সঙ্গে অবশ্য অন্য একটি বর্গ বিশেষভাবে সম্পর্কিত – ঔপনিবেশিক শাসন। ব্রিটিশ আমলই আনিসুজ্জামানের মূল ক্রিয়াক্ষেত্র, এবং এ-ব্যাপারে তিনি মোটেই বেখেয়াল ছিলেন না। তবে, ব্রিটিশ আমলকে স্মরণে রাখা এক কথা, আর একে ঔপনিবেশিক শাসন হিসেবে বর্গীকরণ করা আরেক। ষাটের দশকে উপনিবেশের বাস্তবতার তুলনায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও বিরোধের বাস্তবতাকে বড় করে দেখা ছিল ইতিহাসচর্চার সাধারণ প্রবণতা। উপনিবেশশাস্ত্র আশির দশকে যে-ধরনের প্রগাঢ়তা লাভ করেছিল, ওইসময় তা সুদূরের ব্যাপার। তাছাড়া, ব্রিটিশ শাসন যদি আধুনিকায়নের উৎস হয়ে কলকাতায় মহামহিম রেনেসাঁসের জোগান দিয়ে থাকে, তাহলে একে ঔপনিবেশিক শাসন হিসেবে পাঠ করার কোনো অভ্যন্তর-প্রেরণাও থাকার কথা নয়।
গত কয়েক দশকের জ্ঞানকাণ্ডে আধুনিকতাবিষয়ক ধারণার ব্যাপক রদবদলের অন্যতম কারণ ব্রিটিশ আমলকে ঔপনিবেশিক আমল হিসেবে দেখা। এ-প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকের আধুনিকায়নকে সহজেই পশ্চিমায়ন আর উনিশ শতকের
ভাব-বিপ্লবকে উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার উপজাত হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। দেখার ও পড়ার এ-দৃষ্টিভঙ্গি আনিসুজ্জামানের কালের প্রভাবশালী রীতি-পদ্ধতির তুলনায় এতই আলাদা যে, দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটলে বহু সিদ্ধান্তেরও বদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।
সাহিত্য-পাঠের তরিকায়ও গত কয়েক দশকে বেশ বড় ধরনের বদল ঘটেছে। আনিসুজ্জামান উনিশ শতকের সাহিত্য পাঠ করেছেন এক ধরনের ক্লাসিক মেজাজে – উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বরাভয়ে। সেখানে পাঠের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ দেখা যায়নি। উঁচু শিল্পকলার বিপরীতে নিচু শিল্পকলা নিমেষেই বাতিল হয়ে গেছে। ভাষাভঙ্গির দিক থেকেও তিনি স্বভাবতই অবলম্বন করেছেন সেকালের প্রভাবশালী ধারণা – প্রমিত রীতি অবলম্বনকে প্রগতিশীল অবস্থান হিসেবে অনায়াসেই ঘোষণা করেছেন। শিল্পকলার শ্রেণিবিভাজন আজকাল আর এত নিঃসংশয়ে করা হয় না। ‘নিচু’ হিসেবে আখ্যাত বা শ্রেণিকৃত শিল্পোৎপাদনকে জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক অস্তিত্ব ও পরিচয়ের খুব নির্ভরযোগ্য উপকরণ হিসেবে দেখার কলা ও অভ্যস্ততা মানুষ রপ্ত করেছে। অপ্রমিত উচ্চারণের আধারে মানুষের জিভ ও গলার উষ্ণতা তালাশ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও বিদ্যাজগৎ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সম্মত হয়েছে।
উনিশ শতকের মুসলমান সমাজ নিয়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তেও যথেষ্ট বদল ঘটেছে। এ-বদল একদিকে পরিমাণগত, অন্যদিকে গুণগত। এ-কথা ঠিক, একজন স্থিতধী তরুণ গবেষক হিসেবে আনিসুজ্জামান কেবল প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তই ব্যবহার করেননি, সেকালের তথ্যভাণ্ডারে বেশকিছুর জোগানও দিয়েছেন। কিন্তু কোনগুলো একটি গবেষণায় তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে, আর সেগুলোর ব্যবহারবিধিই বা কী হবে, তা অনেক সময়েই প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাক, ব্রিটিশ আমলের সরকারি নথিপত্রের যে-ধরনের ব্যবহার সাবঅলটার্ন স্টাডিজ দল করেছিল, কিংবা নীলেশ বোস মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ পর্বের ঐতিহাসিক ভাষ্য প্রণয়নের কাজে যে-ধরনের প্রাথমিক উৎসকে মূল্যবান ভেবেছেন, তা আনিসুজ্জামানের তুলনায় বেশ আলাদা। উনিশ শতকের বাংলায় মুসলিম মানস উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি বা তথ্যভাণ্ডারের এ-বদলের একটা বড় কারণ আসলে লক্ষ্যগত পরিবর্তন। পরবর্তীকালের অনেক গবেষকই আধুনিকতা তালাশ না করে, কিংবা সে-আধুনিকতার অগ্রসর নিশানবরদার হিসেবে বাঙালি হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের তুলনা কমিয়ে এনে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন ভেতর থেকে মুসলমানের পরিচয় উদ্ঘাটনের দিকে। ফলে তথ্য-উপাত্তের পরিমাণগত ও গুণগত বদল ঘটেছে।
ওপরে কয়েক দশকের ব্যবধানে যেসব পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইশারা দিলাম, তার নিরিখে উনিশ শতকের মুসলিম মানস পুনর্গঠিত হলে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্ভবত তাকে স্বাগত জানাতেন। এ-প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়তো প্রাসঙ্গিক হবে। একবার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি আমার পিএইচ.ডি সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। উনিশ শতক প্রসঙ্গে সেমিনারে উত্থাপিত এক সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান আপত্তি তুলে বসলেন। সরাসরি স্যারকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি তো এ-বিষয়ে আমাদের ক্লাসে সম্পূর্ণ অন্যরকম সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন। আমার প্রায় হয়ে যাওয়া বিব্রতকর অবস্থাকে অনতিবিলম্বে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত করে শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক উত্তর দিলেন : অধিকতর তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শুধু এ বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তে নয়, আদতে আমার পুরো থিসিসের ক্ষেত্রেই তিনি সমরূপ ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত আমার ভূরি ভূরি সিদ্ধান্তের মধ্যে খুবই গৌণ দু-একটি ছাড়া তিনি আমার মত পরিবর্তনের প্রসঙ্গ তোলেননি। একে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার নিষ্ঠা হিসেবে দেখলে যথেষ্ট হবে না। এ আদতে তাঁর বিশিষ্ট উদারনীতিবাদী মানসিক অবস্থা, যা জীবনের শেষ দশকে পার্টি-ঘনিষ্ঠতা তুলনামূলক বাড়ানোর পরেও অনেকটাই অক্ষুণ্ন ছিল।
চার
দৃষ্টিভঙ্গি বদলের একটা উদাহরণ নেওয়া যাক কথিত দোভাষী পুথির চর্চা থেকে। উনিশ শতকে মুসলমানদের রচনা বলে সাব্যস্ত করা যায় এমন গ্রন্থাদির বড় অংশ লিখিত হয়েছিল এ-রীতিতে। আনিসুজ্জামান অবশ্য প্রধানত আধুনিকতার তালাশ করছিলেন বলে ১৮৭০ সালকে নতুন ধারার সাহিত্যরচনার সূচনা-বছর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ করতে ভোলেননি, এরপরও মুসলমান সমাজে এ-ধরনের পুথি বিস্তর লিখিত হয়েছে। এ-ভাষাকে তিনি বলেছেন মিশ্রভাষা। মিশ্রভাষার মধ্যে বাংলার সঙ্গে, তাঁর এবং আরো অনেকের মতে, মিশেছিল আরবি, ফারসি, উর্দু, তুর্কি ইত্যাদি। এ-সিদ্ধান্তের একটা বড় পরিণতি এই যে, মিশ্রণের অন্য ভাষাগুলো যেহেতু ‘বিদেশি’, কাজেই এ-সূত্রে খুব সহজে বলা সম্ভব যে, মুসলমান সমাজ বাংলাপ্রীতির বদলে ‘বিদেশি’ ভাষার প্রতি অনুরাগে মগ্ন ছিল।
কিন্তু আঠারো-উনিশ সালের ভারতীয় ভাষা-বাস্তবতা আমলে আনলে খুব সহজেই অন্য সিদ্ধান্তের অবকাশ তৈরি হয়। এ-সময় ভারতের প্রধান লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ছিল হিন্দুস্থানি। সে এতটাই যে, ব্রিটিশরাজ উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত নিজেদের আনুষ্ঠানিক স্থানীয় ভাষা হিসেবে হিন্দুস্থানিই ব্যবহার করত। এ-ধরনের প্রভাবশালী একটা ভাষার সঙ্গে বাংলার মিশ্রণ ঘটেছিল – এটাই ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত হয়। অন্য ভাষার শব্দগুলো এ-ভাষার অংশ হিসেবেই বাংলার সঙ্গে মিশেছে। হিন্দুস্থানি এক বিশুদ্ধ ভারতীয় বাস্তবতা – মোটেই বিদেশি চিজ নয়। তদুপরি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই ১৯২৬ সালেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, বাংলায় সরাসরি আদতে আরবি শব্দ মেশেনি – এসেছে ফারসির মধ্য দিয়ে। আসলে বলা উচিত, হিন্দুস্থানির মধ্য দিয়ে। যদি ফারসি থেকেও হয়, তাহলেও বলতে হবে, এ ভাষা-বাস্তবতার মধ্যে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা প্রায় শূন্যের কোঠায়; কারণ, ফারসি বহু শতক ধরে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল। উল্লেখ্য, দোভাষী পুথি প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানির ব্যাপারটা পরবর্তীকালে আহমদ শরীফ সামনে এনেছিলেন।
কাজেই দোভাষী পুথির ভাষাকে মিশ্রভাষা বলার মধ্য দিয়ে একদিকে প্রভাবশালী ভাষা-বাস্তবতাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে, অন্যদিকে যে-ঘটনা বিশুদ্ধ ভারতীয়, তাকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে ‘বিদেশি’ বলে। গবেষক আনিসুজ্জামানের এ-বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয়; কারণ, পুরো থিসিসেই তিনি ভাষাবিষয়ক বিবেচনাটা এ-দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই করেছেন। এর ফলে মুসলমান সমাজ যে প্রধানত ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় ‘বিদেশে’র প্রতি অনুরক্ত হয়ে জীবনযাপন করে, এবং বর্তমানময়তার সঙ্গে তার যে কোনো সম্পর্ক নেই – এ বড় বয়ানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে।
এ-দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থের বহু সিদ্ধান্তের উৎস। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে এখানে অব্যবহিত দুটি পরিণতির কথা বলা যাক। দোভাষী পুথিকারেরা অনবরত দাবি করেছেন, তাঁরা ‘চলতি’ বাংলায় লিখছেন। এ-ধরনের কয়েকটি দাবির কথা আনিসুজ্জামান তাঁর অধ্যায়টিতে উল্লেখও করেছেন। অনেক পরে পুরনো বাংলা গদ্য নামের জরুরি বইটিতে তিনি আদালতের জবানবন্দিসহ প্রচলিত ভাষার যেসব উদাহরণ সংকলন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সেগুলো নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে, পুথিকারদের ‘চলতি’ ভাষার দাবিটি ঠিকই ছিল। ষাটের দশকে এসব তথ্য-উপাত্ত ছিল না। কিন্তু জনগণের ভাষায় জনগণের জন্য লিখছেন – এরকম একটি অসামান্য ঘটনা যে এ-গবেষকের কাছে মোটেই উল্লেখযোগ্য মনে হয়নি, তা এক বিরাট ক্ষতিই বটে।
অন্যদিকে, দোভাষী পুথির মতো ‘প্রাচীনপন্থি’ রচনাদিতে সমকালীনতা থাকতেই পারে না, এরকম একটা মনোভঙ্গি তাঁকে এতটাই চালিত করেছিল যে, তিনি বহুবার এসব রচনাকে জীবনবিমুখতার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। এ-ধারার রচনা নিয়ে গত কয়েক দশকে অসাধারণ সব সন্দর্ভ রচিত হয়েছে। ষাটের দশকের জ্ঞানকাণ্ডে সে-ধরনের কিছু ছিল না। কিন্তু অন্তত গৌতম ভদ্র ঈমান ও নিশান বইয়ে যে-ধরনের পুথিজাতীয় রচনার ভিত্তিতে ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন, সে-ধরনের বেশকিছু দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে ছিল। কিন্তু তিনি সেগুলো ব্যবহার করতে পারেননি।
নিঃসন্দেহে ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রেক্ষাপটে পুথিসাহিত্য পড়ার ও বিবেচনার যে-ছাঁচ তৈরি হয়েছিল, আনিসুজ্জামান তাকেই অনুসরণ করেছিলেন। বিশ শতকের গোড়ায় মুসলমান ভদ্রলোকসমাজ প্রমিত ভাষা রপ্ত করার পটভূমিতে দোভাষী পুথি একবার ব্যাপকভাবে সামষ্টিক তিরস্কারের মুখে পড়ে। চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের আবহে স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তার প্রবলতায় ওই মনোভঙ্গি বদলে গিয়ে পুথির আদর-আপ্যায়ন বেড়ে গিয়েছিল। ষাটের দশকে বিপরীত একটা মনোভঙ্গি দোভাষী পুথির পাঠকে আবার বিপরীতক্রমে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থের ‘দোভাষী পুথি’ চরিত্রটি এই শেষোক্ত পর্বের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।
পাঁচ
ইংরেজ আমলে শাসকপক্ষের সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক কেমন ছিল – এ-প্রশ্নে মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য প্রভাবশালী প্রচলিত মতের অনুসরণ না করে নতুন দিশা দেখিয়েছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার ক্ষেত্রে নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সামনে আনার কৃতিত্বও এ-বইকে দিতে হবে। তার একটি মুসলমান সম্প্রদায়ের জমিদারি হারানোবিষয়ক। প্রচলিত মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মুসলমানরা জমিদারি হারিয়েছিল। আনিসুজ্জামান দেখিয়েছেন, এ-গল্প সত্য নয়। পুরনো জমিদারির অবসান হয়েছিল। নতুন বাস্তবতায় নতুন জমিদারি পত্তনের আর্থিক সক্ষমতা শুধু হিন্দুদেরই ছিল। তারচেয়ে বড় কথা, মুসলমান আমলেও জমিদারি আসলে হিন্দুদের হাতেই ছিল, মুসলমানদের হাতে নয়। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি মুসলমানদের ইংরেজি পড়া সম্পর্কিত। আজতক জোরালোভাবে প্রচলিত ধারণা হলো, মুসলমান সমাজ ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার বশবর্তী হয়ে ইংরেজি শেখায় বিমুখ ছিল। সেরকম প্রচারণা যে তখনকার সমাজে ছিল না তা নয়। কিন্তু আনিসুজ্জামান বারবার এ-বিষয়ে সাবধান করেছেন, মূলত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের আর্থিক সামর্থ্য না থাকার কারণেই মুসলমানরা ইংরেজি শেখায় অগ্রসর হতে পারেনি। তার প্রমাণ, বিচিত্র খাতে প্রথম থেকেই শাসকপক্ষের সঙ্গে মুসলমানদের সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। এ দু-মতই পরে আহমদ শরীফ প্রচার করেছিলেন। তিনি সম্ভবত ধারণাগুলো আদিতে পেয়েছিলেন মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য বই থেকে। আর নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আনিসুজ্জামান ধারণাগুলো পেয়েছেন অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের কাছে। সে যাই হোক, প্রবলপ্রতাপ মতের বিপরীতে অন্য মত গ্রহণ করা এবং তার বৈধতা প্রতিপাদনপূর্বক বয়ান পুনর্নির্মাণ করা দায়িত্বপূর্ণ গবেষকের প্রমাণ বইকি।
কিন্তু এ-বইয়ের এক পুনরাবৃত্ত দাবি – মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি শাসক ইংরেজের স্বতন্ত্র কোনো বিরূপতা ছিল না – সন্দেহাতীতভাবে ইতিহাসের ‘অর্ধ-সত্য’। এ-দাবিতে শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক এতটাই নিষ্ঠ ছিলেন যে, সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের নগণ্য সংখ্যা বিষয়ে হান্টারের উদ্বেগ খণ্ডানোর জন্য তিনি উত্তর ভারতে মুসলমানদের তুলনামূলক বহুগুণ বেশি চাকরির কথা তুলেছেন। যোগ্য প্রার্থী ছিল না বলে, অর্থাৎ ইংরেজি শেখেনি বলে বাংলার মুসলমানরা চাকরি পায় নাই, সে-কথা সত্য। কিন্তু শাসকপক্ষ থেকে শুরু করে স্থানীয় হিন্দু এলিট পর্যন্ত সবার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অংশগ্রহণে ভারতীয় মুসলমান সমাজের যে ব্যাপক অপরায়ণ ঘটেছিল, সে-কথা উল্লেখ না করলে পূর্বোক্ত ‘অর্ধ-সত্য’ মিথ্যার আকার নেয়। উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়া হিসেবে খুঁটিয়ে কালটিকে বিচার না করলে এ-ছবিটা খুব স্পষ্ট করে ধরা না-দেওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু মুসলমানদের অপরায়ণের একরাশ সংবাদ ষাটের দশকের আগেই যথেষ্ট প্রচারিত ছিল। তাহলে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের থিসিসে তা প্রায় অনুপস্থিত কেন?
মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য আধুনিকায়নকে প্রগতির একমাত্র স্মারক হিসেবে সাব্যস্ত করেছে, আর আধুনিকতার সফল আত্মস্থকারী হিসেবে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের সঙ্গে সমন্বিত হওয়াকেই মুসলমান সমাজের প্রধান গুণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এহেন চিহ্নায়নই প্রাগুক্ত অনুপস্থিতির প্রধান কারণ। একই কারণে এ-বইয়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ হয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর। হিন্দু-স্বাতন্ত্র্যবাদ বিষয়টি প্রায় উহ্য থেকে গেছে। উনিশ শতকের শেষাংশ ও বিশ শতকের প্রথমাংশের কোনো কোনো মুসলমান লেখকের সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে তিনি হিন্দু সমাজের অনুরূপ মনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার উৎস, বিস্তার ও গভীরতা সম্পর্কে এ-গবেষণায় জরুরি বহু আলাপ অনুপস্থিত।
ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করেছিল সরাসরি মুসলমানপক্ষ থেকে। শাসনকাজের স্বাভাবিক সূত্র অনুযায়ী পূর্ববর্তী শাসকদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার ফিরিস্তি নির্মাণ খুব জরুরি, আর ইংরেজরা তা-ই করেছিল। স্থানীয় এলিট হিন্দু সমাজ তাতে পরিপূর্ণ সমর্থন ও উৎসাহ জুগিয়েছে। বস্তুত ব্রিটিশ-ভারতীয় ইতিহাস গড়ে উঠেছিল এ-ধারণার ভিত্তিতে যে, ভারতীয় মুসলমান শাসন কেবল অন্ধকারাচ্ছন্ন আর পশ্চাৎপদ নয়, নৈতিক দিক থেকেও দূষিত। কাজেই ভারতীয় হিন্দুর পতনের মূল কারণ ‘বিদেশি’ মুসলমানরা। পুরো উনিশ শতক জুড়ে এ-মনোভাবই আমরা কলকাতার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সর্বত্র প্রতিফলিত হতে দেখি। গবেষকগণ দেখিয়েছেন, স্থিতধী রামমোহন, বিদ্রোহী ডিরোজিও, হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদী বঙ্কিমচন্দ্র – কারুরই এ-বিষয়ে কোনো ভিন্নমত ছিল না। কিন্তু আনিসুজ্জামান এ-ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি দেখেছেন শুধু উনিশ শতকের শেষভাবে, যখন হিন্দু পুনর্জাগরণের একটা আন্দোলন চলছিল। রেনেসাঁসের পরে রেস্টোরেশন – এ-ছক মান্য করেই সম্ভবত তিনি এ-সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কলকাতার উনিশ শতক পাঠ করার ক্ষেত্রে ছকটি বেশ জনপ্রিয়ই বটে। তবে এ-ছক ধরে মুসলমানদের হাল-সাকিন ও সাহিত্যকর্মের খবর নেওয়ার অন্য সংকট আছে।
আনিসুজ্জামান যথার্থই খেয়াল করেছেন, ১৮৭০-এর দশকের গোড়ায় একদিকে মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার নতুন পর্ব শুরু হয়েছিল, অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্যে তাদের অনুপ্রবেশও ঘটেছিল। সাহিত্য, চিন্তা ও সংস্কৃতিতে মুসলমানবিদ্বেষজনিত সাম্প্রদায়িকতার প্রবলতা সত্ত্বেও এ-সময় উঠতি মুসলমান ভদ্রলোকশ্রেণির সঙ্গে প্রভাবশালী হিন্দু মধ্যবিত্তের একটা সমঝোতার সম্পর্কই আমরা দেখতে পাই।
বিশের দশকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতি, দাঙ্গা ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা বেড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি ও সহানুভূতির নানা নজির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯), বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) প্রমুখ এ-দৃষ্টিভঙ্গির ভালো প্রতিনিধি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দশের দশকের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে লেখা বহু-উদ্ধৃত প্রবন্ধ, এবং আগে-পরে লেখা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলো এ-সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল রচনা; চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) ও সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) চিহ্নিত হতে পারেন রাজনৈতিক প্রতিনিধি আর অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনের যৌথতা ও বেঙ্গল প্যাক্টকে বলা যেতে পারে সমধর্মী রাজনৈতিক কর্মসূচির বহিঃপ্রকাশ।
ওই প্রজন্মের বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করলেই বোঝা যাবে, সমন্বয়বাদিতাই প্রধান যুগধর্ম। শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮), মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ
(১৮৬১-১৯৩৩), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩), মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) প্রমুখ এ-যুগের প্রতিনিধি। এঁদের অনেকেই সমন্বয়বাদী ছিলেন – বস্তুত অধিকাংশ; আর কয়েকজন ছিলেন রীতিমতো জাতীয়তাবাদী-কংগ্রেসি। সবাই পত্র-পত্রিকা বের করেছেন। স্বজাতির কল্যাণ কামনায় কাজ করেছেন। এ-স্বজাতি মুখ্যত বাঙালি মুসলমান; আর প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অগ্রসর বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে ঐক্যের মেজাজই প্রধান ছিল। ব্যতিμমহীনভাবে সবাই বাংলায় লিখেছেন। আর এঁদের সবার বাংলা প্রমিত; অনেকেরই বঙ্কিমীয় ও রাবীন্দ্রিক – তৎসমবহুল। এক কথায় একে বলা যায় সমন্বয়ধর্মী বাংলা, বাঙালি মুসলমানের তরফে যে-বাংলার প্রবর্তন করেছিলেন বস্তুত মীর মশাররফ হোসেন।
মুসলমান-সমাজ সংখ্যাগুরুর রাজনীতিতে প্রবেশ করার আগের দশকগুলোতে বিকশিত ‘বাঙালি’ ও ‘ভারতীয়’ জাতীয়তাবাদ এবং ‘অসাম্প্রদায়িক’ সমন্বয়বাদের ওই অসাধারণ যুগটিকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব না, যদি উনিশ শতকের কলকাতায় হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের আধুনিকায়নের উত্থান-পতনের পথরেখা ধরে পুরো ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করতে চাই। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থের এ-অংশটি, আমাদের বিবেচনায়, এ-কারণেই সন্তোষজনক হয়নি।
ছয়
আগেই বলেছি, উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের মনোজগৎ ও সাহিত্য বিশ্লেষণের জন্য ভারতীয় মুসলমান, বাংলা অঞ্চলের অবাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু – অন্তত এ-তিনটি বর্গের সঙ্গে সম্পর্ক পরীক্ষা করা জরুরি। একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, এটা গভীরভাবে শ্রেণিগত প্রশ্ন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বেশকিছু ক্ষেত্রে, যেমন বাঙালি মুসলমানের ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণ-প্রশ্নে, আর্থিক সংগতির কথা মনে রেখেছেন। কিন্তু নানা লক্ষণ থেকে মনে হয়, এ-ব্যাপারে আরো বেশি মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। মুসলমান সমাজের সংস্কার আন্দোলন কেন আবশ্যিকভাবে ধর্ম-সংস্কার-আন্দোলনে রূপ নিল, তার ব্যাখ্যা শ্রেণি-প্রশ্ন বা কৃষক-প্রশ্ন ছাড়া পাওয়া যাবে না। ঠিক তেমনি বাঙালি মুসলমান সমাজের নেতারা প্রায় সবাই কেন উর্দুভাষী ছিল, তার ব্যাখ্যাও আসলে শ্রেণিগত। শুধু মতাদর্শ আর মনোজগতের বরাত দিয়ে এসবের কিনারা করতে যাওয়াকে জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকটই বলতে হবে।
উল্লেখ্য, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থসহ এ-বিষয়ের প্রভাবশালী প্রায় সব সন্দর্ভেই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তুলনামূলক কম গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতীয় মুসলমানরা যে ব্যাপকভাবে সংখ্যালঘু, ফলে তাদের সামষ্টিক মনস্তত্ত্ব ও প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সে-অবস্থার প্রতিফলন ঘটবে, সে-কথা মোটের ওপর অনুল্লিখিতই থাকে। আগের শাসক ছিল মুসলমান, আর ব্রিটিশদের সঙ্গে দেন-দরবারে মুসলমানরা প্রায় সমান প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদের উপস্থিত করতে পেরেছিল – প্রধানত এ-দুই কারণে প্রায় সমস্ত আলোচনায় সংখ্যালঘুতার গুরুতর দিকটা এড়িয়ে যাওয়া হয়। বাঙালি মুসলমানের উত্তর ভারতপ্রীতি, উর্দুপ্রীতি ইত্যাদিকে আদতে সন্তোষজনকভাবে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যাবে না, যদি সর্বভারতীয় সংখ্যালঘুতা বিষয়টিকে আড়াল করে কেবল মানসিক পশ্চাৎপদতাকে মুখ্য করে তোলা হয়। তার চেয়ে বড় কথা, উনিশ শতকের ‘বাঙালি’ ধারণাটি বিশুদ্ধত হিন্দু-কল্পনা, আর মুসলমানের তরফে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাট দশকের মামলা। এমতাবস্থায় বাংলাভাষাপ্রীতিকে কেন্দ্রীয় বর্গ স্থির করে দেশপ্রেম ও প্রগতিশীলতা বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ শুধু যে ওইকালের ভাষা-পরিস্থিতির প্রতি অমনোযোগ প্রমাণ করে তা নয়, এটা আসলে পরিষ্কার কালাতিμমী দোষ।
অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বলা যায়, তিনি সেকালের প্রভাবশালী মতামত দ্বারাই মুখ্যত চালিত হয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হলো, তিনি শুধু সে-মতামতের ভোক্তা ছিলেন না, নিজেও তার পোষকতা করেছেন, এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভাষার জোগান দিয়েছেন। তাঁর অর্জনের যথার্থ ব্যবহার হবে তখনই, যখন একে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে আমরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, কৌশল আর তথ্য-উপাত্তের নিরিখে নতুনতর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। তার জন্য মনে রাখা দরকার, ইতিহাস-পাঠে ‘সত্যমূলকতা’ তুলনামূলক গৌণ ব্যাপার। কারণ, ইতিহাসে আমরা বস্তুত বর্তমানকেই পাঠ করি। আনিসুজ্জামান তাঁর কালের প্রগতিশীল ও প্রয়োজনীয় ভাবধারা হিসেবে জাতীয়তাবাদ অবলম্বন করেই বয়ান নির্মাণ করেছেন। সেকালের পটভূমিতে জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য উত্তম বিবরণী হাজির করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেজন্য তিনি পর্যাপ্ত প্রশংসাও পেয়েছেন।
কিন্তু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উদারনৈতিক অবস্থান, আধুনিকতাবাদ এবং প্রগতিশীলতাও বিশেষ স্থান-কালের বাস্তবতা দ্বারাই চালিত হয়। এ প্রত্যেকটি বর্গের সাধারণ সীমাবদ্ধতা এই যে, সুবিধাপ্রাপ্ত তুলনামূলক শিক্ষিত-নাগরিক জনগোষ্ঠীর ভিত্তিতেই এ-বর্গগুলো কাজ করে থাকে। আরো বেশি পরিমাণে মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং বিবেচনার গণ্ডিতে আরো অনেক বেশি মানুষকে নিয়ে আসার কথা আমাদের ভাবতে হবে। এটা একদিকে বর্তমান রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে ইতিবাচক অর্থে প্রভাবিত করার মামলা, অন্যদিকে জ্ঞানতাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত নতুন অর্জনগুলোকে আত্মসাৎ করে বয়ানকে তুলনামূলক পূর্ণাঙ্গ করে তোলার অভিযাত্রা। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্পর্কে যতটা ভাবা যায় তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, তিনি এ-ধরনের অভিযাত্রাকে নিঃসংকোচে স্বাগত জানাতেন।
[১৬ মে ২০২৫ তারিখ আনিসুজ্জামানের মৃত্যুবার্ষিকীতে কালি ও কলম আয়োজিত ‘অধ্যাপক আনিসুজ্জামান স্মারক বক্তৃতা’ হিসেবে পঠিত]
লেখক : কবি ও সাহিত্যিক